শাইনি শিফা’র ভ্রমণ কাহিনীঃ নদীর নাম শঙ্খ আর ঝর্ণার নাম রেমাক্রি
- Update Time : শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩
- ৮০৪ Time View



যদি নদীর নামটা হয় শঙ্খ আর ঝর্ণার নাম রেমাক্রি….তাহলে কি আর সেটা দেখার লোভটা সামলানো যায়???
আমরাও পারলাম না।
আমরা মোট ১১ জন। রাতের বাসের টিকেট কাটা হলো। কারন, চাকুরীজীবিদের জন্য এটাই সুবিধা হয়। সারাদিন কাজ শেষ করে বাসে চেপে বসলেই গন্তব্য।
আমরাও হাত ব্যাগে টুকটাক খাবার নিয়ে রওনা দিলাম বান্দরবানের উদ্দেশ্যে। সকালে পৌঁছলাম বান্দরবানে। সেখানে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে আবার বেরিয়ে পড়লাম।
বান্দরবান পার হয়ে প্রথমে মেঘলা।
মেঘলা নামটা শুনলেই মনের মধ্যে যেন একরাশ মেঘ এনে ভর করে। গিয়ে দেখলামও তাই। মেঘলার আকাশ পরিষ্কার তবে মেঘ আছে কিছু কিছু জায়গায়– দেখে মনে হলো, সাদা রং দিয়ে কেউ নীল আকাশে ছোপ ছোপ মেঘ এঁকে রেখেছে। নিচে টলটলে পানির মত আয়নায়ও দেখা গেল সেই নীল আকাশে সাদা মেঘের ছোপ। মনটাও সাদা তুলোর মত ফুরফুরে হয়ে উঠলো।
চারপাশের পাহাড়গুলো হরেক রকমের সবুজ পাতায় ছাওয়া। সবুজেরও কত রকম শেড থাকতে পারে — সেটা দেখে মুগ্ধ হলাম কিছুক্ষণ। গাছের পাতাগুলো দেখে হলো, এইমাত্রই হয়তোবা কেউ সেই টলটলে পানি দিয়ে মুছে দিয়ে গিয়েছে যেন। টলটলে পানির উপরে টলমলে সেতু। সেই ঝুলন্ত সেতুতে ঝুল খেয়ে পাখির মত ডানা মেলে দিলাম শূন্যে।
মেঘলা দেখা শেষ করে চললাম চিম্বুকের শৈলপ্রপাত দেখতে। অসাধারন সেই শৈলপ্রপাত।
আমাদের মধ্যে দু’তিনজন সেই শৈলপ্রপাতে নামবেই নামবে।
বড় বড় পাথরের মাঝখান দিয়ে বরফ গলা পানি ছুটে চলেছে নিরবধি। পাথর ধরে ধরে মোটামুটি হামাগুড়ি দিয়েই চললাম জলপ্রপাতের কাছে। কাছাকাছি যেতে না যেতেই সামনে দেখি আমার এক দেবর পপাত ধরনীতল। পিছলে পিছলে পানির স্রোতে চলে যাচ্ছে অনেক দূরে। দেখে বুকটা ধড়াস করে উঠলো। সে নিজেই নিজের তাল সামলাতে পারছে না। ঝর্ণা ওকে পাঁজা কোলা করে নিয়ে যেতে যেতে পাথরের গায়ে থেমে গেল একসময়। বেচারা দেবরজী!
শৈলপ্রপাতের সৌন্দর্য আমাদেরকে বেশিক্ষণ বেঁধে রাখতে পারলো না। কারন ২০০৩ সালের দিকে ওটার সৌন্দর্য আমরা বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করে ফেলেছি।
উপরে উঠে এলাম। উপর মানে পিচঢালা রাস্তায়। সেখানে একটু জিরোতে গিয়ে আদিবাসীদের হাতে তৈরী একটা থামিও কিনে ফেললাম। ওদের কাছ থেকেই শিখে নিলাম — কিভাবে সেটা পড়তে হয়।
আবার চললাম সমুখ পানে।
প্রথমে নীলগিরি, নীলগিরি পার হয়ে তবেই থানচি। দুপাশে পাহাড় ঠেলে ঠেলে এঁকেবেঁকে রাস্তা চলেছে আমাদের গাড়ি। পাহাড় কেটে কেটে এমন পথ তৈরী করেছে যারা, যারা আমাদেরকে পাহাড়ের চূড়া দেখার সুযোগ করে দিয়েছে — মনে মনে তাদেরকে ধন্যবাদ আর ভালোবাসা জানালাম।
পাহাড়ের চূড়ায় আরেক পাহাড় থানচি। যেন অন্যসব পাহাড়গুলোকে শাসন করছে সে।
মেঘ আর কুয়াশার লুকোচুরি খেলা চলে পাহাড়ের গায়ে। দমকা হাওয়া এসে খেলাটা লন্ডভন্ড করে দিয়ে যায়। মেঘেরা আবার আসে, পাহাড়কে ছেড়ে যেতে পারে না। পাহাড়ের সাথে সখ্যতা আর প্রেম তার কাটে না। এ কি কুয়াশা না কি মেঘ!! আমি অবাক হয়ে ওদের খেলা দেখি। নাকে এসে লাগে বুনো গন্ধ। সেই মাদক গন্ধে আমিও মাতাল হই পাহাড়, কুয়াশা আর মেঘেদের সাথে।
থানচি পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা গড়িয়ে আসে। মেঘেরা ঘুমোতে যায়। পাহাড় কালো হতে থাকে। মন খারাপেরা ভর করে রাত্রি নামে পাহাড়ের কোলে। আমরা থানচির গেস্ট হাউজে গিয়ে উঠি। ওখানেই বনমোরগ, বাম্বু চিকেন, হলুদ ফুল ভাজি আর বাঁশ কোরল দিয়ে ভাত খাই। (বাঁশের মাথার দিকে কচি বাঁশকে ওরা বাঁশ কোরল বলে।)
পরদিন সকালে তড়িঘড়ি নাস্তা করে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি ‘বড় পাথর’ আর ঝর্ণা দেখার লোভে। পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে নিচে এসে দুটো নৌকা নিয়ে নিই আমরা। ছোট ছোট ডিঙি নৌকা।
নদীটা মন কেড়ে নেয় তার নিজস্ব সৌন্দর্য দিয়ে। মাঝির কাছ থেকে জানতে পারি নদীর নাম ‘সাংগু’—- বাংলায় এটাকে বলে শঙ্খ নদী। নামটা শুনেই মনে হল খুব আদুরে নদী। শঙ্খ নদী পাথরে ভরা, অল্প স্বল্প স্বচ্ছ পানি। পাথরগুলো যেন চেয়ে আছে আমাদের দিকে। ছোট, বড়, মাঝারি, কালো, ধুসর, দুধসাদা… হরেক রকমের পাথরে ভরা সাংগু।
পাথরগুলোকে একটু ছুঁয়ে দিয়ে আদর করে বললাম,
” তোরা থাক, আমরা আসছি ঘুরে”।
ডিঙি নৌকা বেয়ে যেতে লাগলো পাহাড়ের খাঁজ ধরে। কি টলটলে স্বচ্ছ পানি!
দুইপাশে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা ছোট ছরার মত বয়ে চলেছে শঙ্খ। ঘন্টাখানেক চলার পরে নদীর পাথরগুলো যেন আরও উপরে উঠে এল। আমাদের এতটা ভার সে সইবে কেন? বড় আল্লাদী যে সে। নামতে হলো অগত্যা। নদীর দুই পাড়েও শুধু পাথর আর পাথর। পাথর মাড়িয়ে চলতে থাকি আমরা। কারো আবার দুই পাথরের মাঝখানে পা আটকে যায়। যেন ওরা ডেকে বলছে, ” তুই এখানে থেকে যা”।
কিছুটা পথ বেয়ে টং দোকানের পাহাড়ী কলা আর পাহাড়ী পেপে খেয়ে আবার উঠি নৌকায়। ‘বড় পাথর’ এ এসে দেখি আসলেই অনেক বড় একটা পাথর। এখানকার লোকজন এটাকে পূজা করে। পাথরের গায়ে বলি দেয় বন মোরগ। রক্তও দেখলাম ছোপ ছোপ। মনেহল, সিনেমায় দেখা বনমানুষের বলি দেয়ার দেশে চলে এসেছি।
বড় পাথর পার হয়ে আরো ঘন্টাখানেক পরে ঝর্ণার কাছে গিয়ে পৌছলাম। ঝর্ণাটার নাম রেমাক্রিখুম। বাংলাটা আর জানা হলো না। তবে খুম মানে মারমা ভাষায় জলপ্রপাত। ঝর্ণাটা ছোট কিন্তু আবেদনটা অনেক বেশি। ছোট জিনিসের আবেদন সবসময়ই মনেহয় একটু বেশিই হয়। নয়তো ভ্রমর, প্রজাপতি বা চন্দনা নিয়ে এত গান বা কবিতা রচনা হতো না, রচিত হতো ঐ বাজপাখি বা উটপাখি নিয়ে।
ঝর্ণার কাছে গিয়ে অনেক্ষণ সখ্যতা হলো। বাচ্চারা রেমাক্রিখুমের জলে স্নান করলো। আমি কিছুক্ষন একটা পাথরের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে রইলাম। যেন ওর সৌন্দর্যকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা। ঠান্ডা পানিতে পা ভিজাতে উদগ্রীব আমরা সবাই। পাথরগুলো বড্ড বেহায়া। একটু এদিক সেদিক হলেই আমাদেরকে শুইয়ে দিচ্ছে। আমরাও পিছলে গিয়ে হেসেই মরে যাচ্ছি। একটু দূরেই আমার দেবরের বাচ্চা আর বাচ্চারা সেই পানিতে গোসল করা শুরু করে দিল।
আমি কেবল শুয়ে শুয়ে ওদের জলকেলি দেখি, জলের হলিখেলা দেখি আর মাথার উপরে নীল – সাদা মেঘেদের লুকোচুরি খেলা দেখি। এদের এতটা সৌন্দর্য আমি একসাথে গোগ্রাসে গিলতে পারি না। আমার কি সাধ্য আছে স্রষ্টার অপরূপ সৌন্দর্যকে বর্ণণা করার!!! এতটা মেধা বা কলমের শক্তি আমাকে তিনি দেন নি।
রেমাক্রিখুমের পরে আরও তিনঘন্টা পায়ে হাঁটার পর পাওয়া যেত নাফাখুম ঝর্ণা যেটা কিনা পাঁচ স্তরে বেয়ে গিয়ে ২৫/৩০ ফুট নিচে গিয়ে পড়েছে। নাফাখুমকে বাংলাদেশের নায়াগ্রা বলা হয়। সেখানে যাওয়ার আর সময় পেলাম না আমরা।
রেমাক্রি আমাকে বাকি দু’টো দিন আচ্ছন্ন করে রাখলো। যেখানে যাচ্ছি… যা ই খাচ্ছি —- রেমাক্রিকে মাথা থেকে তাড়াতেই পারছি না। তারপর রেমাক্রিকে পেছনে ফেলে শঙ্খ নদী আর পাহাড়ের সবটুকু সৌন্দর্য গিলতে গিলতে থানচি বিজিবি রিসোর্টে এসে পৌছাই। এসে দেখি, ওমা! আমি যেই কটেজে থাকি সেটার নামই তো রেমাক্রি। তারপর রাতে সেই রেমাক্রির কোলেই ঘুমিয়ে পড়ি আমি।
শাইনি শিফা
কবি, লেখক ও
আবৃত্তিকার( বাংলাদেশ বেতার)















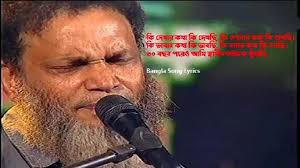


.পাহাড়ি এলাকার ভ্রমণ কাহিনী পড়ে অনেক ভালো লাগলো।ছোটবেলায় রাঙ্গামাটি এলাকায় বসবাস করেছি বলে সেখানকার প্রকৃতি পরিবেশ এর বর্ণনা এই লেখনীতে পড়ে বেশ ভালো লাগলো ৷অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এই মনোগ্রাহী লেখনির জন্য ৷